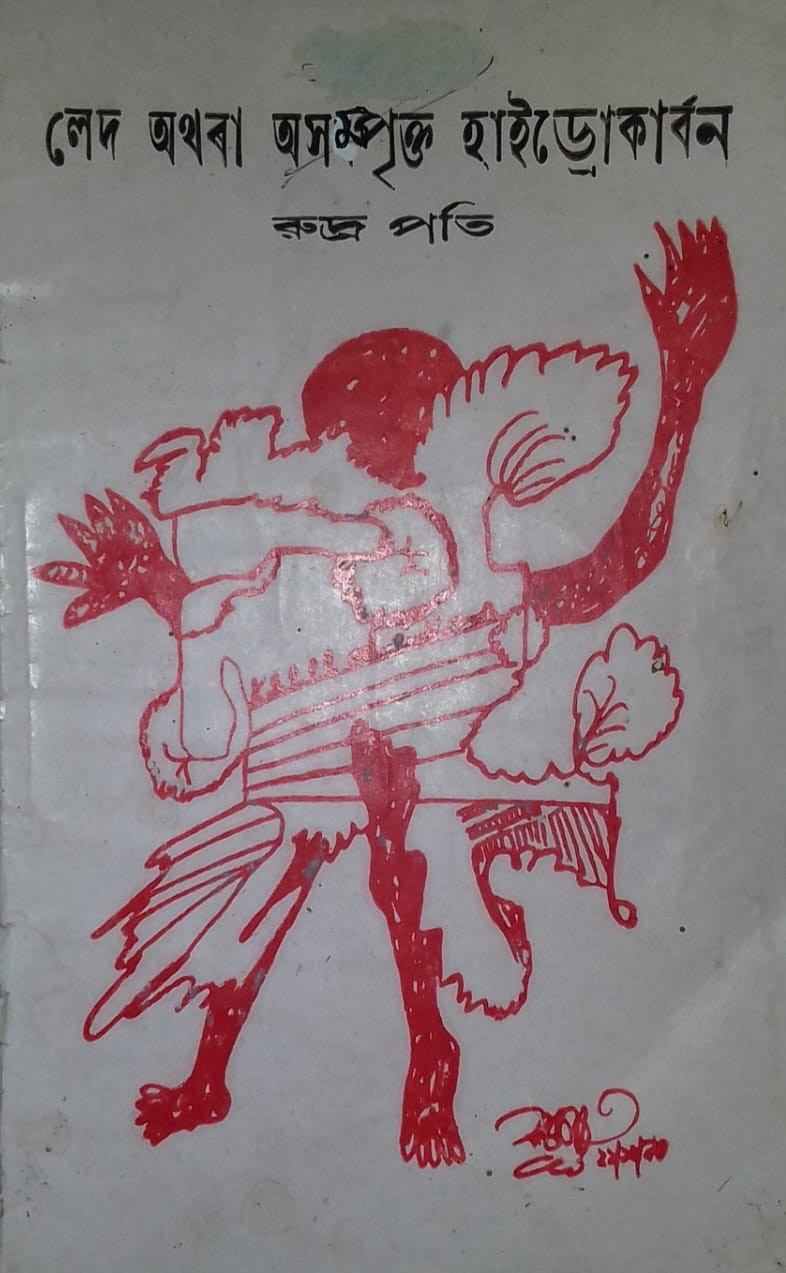রুদ্র পতি - বাংলা কবিতায় প্রান্তিক চাষার স্বর
ড. সুপ্রিয় দেওঘরিয়া
রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতায় বেশ কিছু বাঁক বদল এসেছে। অনেক কবি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছেন তাঁদের নির্দিষ্ট শৈলীতে এবং বিশেষতায়। সাম্প্রতিক কবিতা চর্চার যে দুটো দশক আমার বিশেষভাবে ভালো লাগে তা অবশ্যই সত্তর এবং নব্বইয়ের দশক। এই দুই দশকেই নিজস্বতায় পরিপূর্ণ বেশ কিছু দক্ষ কবির সাথে পরিচিত হতে পারি। বিশেষকরে নব্বইয়ের দশকের কবিদের মধ্যে কারো লেখায় ফুটে উঠেছে দেশভাগের যন্ত্রণা, উদবাস্তু সমস্যা। কারো লেখায় ফুটে উঠেছে নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। কেউ ছন্দে একাকার হয়েছেন। আবার কেউ বুক চিতিয়ে শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে মফস্বলের লড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। প্রত্যেককে নিজের ক্ষেত্রে সম্মান জানিয়ে, একটা কথা এখানে বলতেই পারা যায় যে নব্বইয়ের দশকের আর কোনো কবি শুধুমাত্র 'অমরত্ব' পাবার আশায়, আলেয়ার মতো এক অমোঘ মোহতে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে, কবিতার কলমকে করে তুলেছিলেন লাঙ্গলের ফলা, নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন এক প্রান্তিক চাষী হিসেবে, লিখেছিলেন --
"মাটি ফাটার দিন ; বুকও ফেটেছে...
#
ফাটুক;
এই ফাটা -পথ দিয়েই
আষাঢ়ের জল ঢুকবে।"
( বৈশাখ,১.প্রতীক্ষা,প্রান্তিক চাষা)
হ্যাঁ আমি রুদ্র পতির কবিতাই বলছি। যিনি নিজস্বতা নিজের রচনা শৈলীতে এবং নিজের কবিত্বের বিশ্বাসে অটুট ও আশাবাদী এক বিস্ময়! তাঁর দুরন্ত আগমন, দাপিয়ে বেড়া এবং এক নির্জন সন্ন্যাস আমাদের তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রলোভিত করে।
গ্রাম্য কবি,মেঠো কবি ,চারণ কবি - কবিতার ক্ষেত্রে এ নামগুলি আমাদের কাছে অনেকবার এসেছে । বৃহত্তর বাংলা কবিতায় এবং বিশ্ব সাহিত্যে শুধুমাত্র গ্রাম্য জীবন এবং গ্রামকে কেন্দ্র করে কবিতা অনেক লেখা হয়েছে। গানের ক্ষেত্রে সম্প্রতিক সময়ে 'নাগরিক রাখাল' নামে একটি শব্দ-বন্ধ খুব প্রচলিত। আবার চরণ কবি বৈদ্যনাথ বা পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের নামও আমরা অনেক শুনেছি। জসীমউদ্দীনের কবিতায় এই গ্রাম বাংলার যে ছবি ফুটে ওঠে, পল্লী জীবনের মানুষের ছোট খাটো যন্ত্রণা-আনন্দ-ভালবাসা, তা এক কথায় অসামান্য। স্কটল্যান্ড এর বিখ্যাত জাতীয় কবি রবার্ট বার্নসকে প্লাওম্যান পোয়েট বলা হয়। এই প্লাওমেনের সাথে লাঙ্গলের সম্পর্ক ওতপ্রতভাবে জড়িত। ঠিক সেইরকমই নব্বইয়ের দশকের এই কবি নিজেকে অদ্ভুত এক অভিধায় অভিহিত করলেন -'প্রান্তিক চাষা' হিসেবে । নিজেকে ঘোষণা করলেন 'মার্জিনাল পোয়েট' হিসাবে। নিজের জীবনকে এই কথায় তুলে ধরলেন কবিতার আঙিনায়। ভাদরিয়া ঝুমুরের কবি যেমন নিজেদের সুখ দুঃখ নিজেদের সুরে আঙ্গিকে তুলে ধরেন ঠিক তেমনি এই কবি বাংলার অসংখ্য ম্যাগাজিনে লিখলেন ক্ষেতের আলের কথা, গ্রাম নির্ভর ভারতের ভারতবর্ষের কথা, মুখে ফুঁ দিয়ে লন্ঠনের কাচ মোছার গল্প, বিদ্যুৎহীন ভারতবর্ষের কথা, খাবার ঘর শোবার ঘর এক করে দেওয়ার কথা -
"আমাদের খাবারঘর শোবার ঘর একটাই বলে
ভারতবর্ষের আয়তন ছোট মনে হল"
(অসহায়তা, এবছর শ্রাবণ ভালো )
রুদ্র পতির কবিতা লেখার শুরুটা আশ্চর্য রকমভাবে হয়েছিল। কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা মেধাবী ছাত্র রুদ্র পতি বাঁকুড়া শহরের এক কলেজে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়বার জন্য যান। কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট পছন্দের হলেও শুধুমাত্র গ্রাম্য জীবন, ভলিবল খেলা, সাঁতার কাটা, এগুলো মিস করার জন্য তিনি চলে আসেন প্রত্যন্ত এক গ্রাম্য কলেজে। শুধু বিষয়ের দিক দিয়ে না, অণু পরমানু এবং মৌলের মধ্যে কবি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করেন মানুষের অস্তিত্ব, জীবনের অস্তিত্ব। কবিতায় জীবন এবং কেমিস্ট্রির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন কবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রথাগত শিক্ষার থেকে কবি বেরিয়ে আসতে থাকেন তাঁর নিজের ভেতরের ভাবনাকে কবিতায় প্রকাশ করার তাড়নায়। ব্যাস শুরু হয় অস্থিরতা, শুরু হয় চাঞ্চল্য। শুরু হয় বিভিন্ন কবিতার ম্যাগাজিন পড়া কবিতা পাঠানো কবিতা লেখা। অনেক কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। কোনো রকম বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বা সমাজ মাধ্যম ছাড়াও শুধুমাত্র চিঠিকে ভিত্তি করে এবং ভারতীয় পোস্ট বিভাগের মাধ্যমে বৃহত্তর বঙ্গের সাথে কবির পরিচয় হতে থাকে। একজন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অধ্যাপক বা কেমিস্ট হওয়ার চেয়ে একজন কবি হওয়া রুদ্র পতির কাছে বেশি বড় মনে হয়। কারণ তরুণ রুদ্র পতির মতে একজন কবির " অনেক বেশি বলার আছে, প্রকাশ করবার আছে, আছে নির্মাণ, আছে পরিব্যপ্ত হওয়ার অসীম ক্ষমতা"( রুদ্র পতি : সাক্ষাৎকার, রাহুল গাঙ্গুলী, তরঙ্গ পরিবার)।
একের পর এক পড়ার বিষয়ে বদল আসলে এক প্রকৃত কবির অস্থিরতার লক্ষণ। একজন কবির মধ্যে সৃষ্টির তাড়নায় এই অস্থিরতা স্বাভাবিক। যদিও আমাদের চাওয়া পাওয়ার জগতে এর মূল্য খুব কম। কবি এই সময় আইটিআই পড়েছেন, কেমিস্ট্রিও পড়েছেন। পাশাপাশি চলেছে সাহিত্য চর্চা, কাব্য দেবীর সাধনা। এই অস্থিরতা এবং কাব্য চর্চার জন্য, পড়াশোনায় বারবার ছেদ পড়ার জন্য, কবির জীবনের নেমে আসে বেকারত্ব। শিকড়ের টান আরো গভীর হয়। কবিকে আমরা দেখতে পাই ক্ষেতের আলে, কোদাল হাতে। কবি হয়ে ওঠেন একজন প্রান্তিক চাষা। কেমেস্ট্রি পড়া, আইটিআই এর ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা, বেকারত্ব, গ্রাম্য জীবনের টান, চাষ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং অন্তরের তাড়না, সৃষ্টি সুখের চাঞ্চল্য, তরুণ যুবক রুদ্র পতির মধ্যে জন্ম দেয় দুটি কাব্যগ্রন্থ - "প্রান্তিক চাষা"( সিন্ধুসারস প্রকাশনী, হাওড়া, ১৯৯৩) ও "লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন" (খনন প্রকাশন, নাগপুর, মহারাষ্ট্র ১৯৯৩)। লেদ মেশিনের অসম্ভব ক্ষমতা কবি আশ্চর্য ভাবে দেখেন। কবি আইটিআই পড়ার সময় এই মেশিনের প্রতি আকর্ষিত হন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যন্ত মানুষের জীবনে, গরিব মানুষের জীবনে কেমিস্ট্রির ব্যবহার তিনি যেভাবে দেখেছেন তাও এক কথায় অনন্য। এই দেখার চোখ একদিকে জীবনে বিজ্ঞান অপরদিকে তেমনি জীবনের করুন ব্যঞ্জনা। কবির কথা অনুযায়ী -
"আমরা যখন ১৯৮২ সাল তখন হোস্টেলে পড়াশোনা করতাম ক্লাস নাইনে, রাত্রে হোস্টেল সুপারকে না বলেই চলে যেতাম ঝুমুর নাচ দেখতে, গাজন পরব দেখতে, রাত্রে সেখানে নিভু নিভু আলো জ্বলতো, সেইসব বড় ডিবরির মত লম্ফ সবই জ্বলতো অ্যাসিটিলিনএর সাহায্যে। সেখানে কেরোসিনের ব্যবহার হতো না তখন। কারণ ক্যালসিয়াম কার্বাইড গুড়ো অনেক কম পয়সায় পাওয়া যেত তাতে জল ঢাললেই এসিটিলিন গ্যাস তৈরি হতো। আশ্চর্য প্রান্তিক গরিব মানুষের জীবন দেখেছি আমি। জীবনে সেই প্রথম কেমিস্ট্রির ব্যবহার চিনেছি। যা হলো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন " (রুদ্র পতি, হোয়াটস্যাপ )
এই দুই অভিজ্ঞতার কথা "লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন" বইয়ের কবিতায় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে এক অন্য রকমের শব্দের প্রয়োগ এবং গঠনে কেমিস্ট্রি শব্দ-বন্ধের ব্যবহার খুব কম কবির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। এই কবিতার বইটি সমালোচক মহলে বিশেষ প্রশংসা পায়।
"লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন" কবিতার বইয়ের প্রতিটি কবিতায় যন্ত্র এবং মানবের এক আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। পাশাপাশি লেদ শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। এক প্রান্তিক কবি ঘোষণা করেছেন নিজেকে একজন লেদ শ্রমিক হিসাবে -
" মিথ্যে বর্ণমালা। চাষার ছেলে আমি
বৃষ্টি হীনতায় আজ লেদের শ্রমিক;
কিছুই চাইনা, শুধু চেয়েছি ভেঙ্গে যেতে।"
(তেজস্ক্রিয়তা, লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)
আমরা বিনয় মজুমদারের কবিতায় গাণিতিক ভাষার প্রয়োগ দেখেছি। রুদ্র পতির এই কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন গাণিতিক ভাষা, সিম্বল, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন শব্দ-বন্ধের প্রয়োগ পাওয়া যায়, তেমনি ক্রমাগত "হার্ড" ও "কংক্রিট ইমেজ" এর ব্যবহার এবং অন্তরে একটি দ্রোহের প্রচ্ছন্ন সুর লক্ষ্য করি।
" দেখি ধোঁয়া, কোলাহল; পতাকায় পতাকায়
শোষণের পদ্ধতিগুলি
শুধু বদলে যায়" (রূপান্তর, লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)
এই প্রয়োগগুলির মধ্যে কবির ভাষায় মেধার অসম্ভব প্রয়োগ লক্ষ্য করি -
" গ্রাফাইট এঁকেছে ছবি। ভালোবাসা, তোর মুখ দেখে
মানুষের বিচ্যুতিগুলি মন থেকে বারবার
মুছতে চেয়েছি। " ( ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)
কিংবা লেদের কংক্রিট মেশিনের পাশেও ফুটে ওঠে এক তরুণ প্রান্তিক চাষার চোখের জল। আষাঢ়ের বৃষ্টির জলে চাষ করতে না পারার আক্ষেপ। একটি ছোট্ট কবিতা সম্পূর্ণ তুলে ধরছি-
" লেদ মেশিন এর পাশে আষাঢ় এলো...
#
অনুভূতি আজও মরে যায়নি ব'লে
কেউ কেউ কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে
নোংরা হাত দুটি বর্ষা জলে শুদ্ধ ক'রে নেয়
#
আকাশের দিকে এইমাত্র যে শ্রমিকটি তাকিয়ে ছিল
তার চোখে জল কেন এলো?!
(আষাঢ়, লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)
পাশাপাশি একই সময়ে রচিত " প্রান্তিক চাষা " বইটির কবিতাগুলি একটু অন্য ধরনের। ঠিক একই সময়ে এই দুটি বইয়ের কবিতাগুলি লেখা হলেও, এই কবিতার ভাষা খানিকটা আলাদা, যদিও তা কবির নিজস্ব। এই কবিতার বইয়ের প্রায় অধিকাংশ কবিতার বুনন শৈলী অসম লাইন বিন্যাস ও ছোট ছোট অমিল লাইনে বিভক্ত। কবিতাগুলির মধ্যে একটি ব্যাঞ্জনার সুর পরিলক্ষিত। 'আমি' কেন্দ্রিক শব্দের মধ্যে কবি দেখিয়েছেন এক প্রান্তিক চাষার নিজের কথা। এই কবিতার ভাষা তুলনামূলক ভাবে কোমল, নরম, এবং এক প্রচ্ছন্ন রোমান্টিসিজমের সুর অনুভব করা যায়। কিন্তু এই কবিতাগুলির বক্তব্য কখনো অতীব প্রকট নয়। বরং খানিকটা প্রচ্ছন্নই বলা চলে। দুঃখ,বেদনা, ভালবাসা, কোমলতার ছবি ধরা পড়েছে কবিতার ছত্রে ছত্রে। এবং শেষ পর্যন্ত কবিতা গুলি, কবির নিজস্ব কবিতা হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেনি- বরঞ্চ সার্বিকতা লাভ করেছে বলা যায়। বেশ কয়েকটি কবিতার লাইন তুলে ধরছি এখানে -
"যতই তার বিঁধে যাক রাত ও দিনে
পাখির পাখায় তবু অজস্ৰ বাতাস
ঠোঁটে ঠোঁটে খড়কুটো, শস্যবীজ রাখা"
( আবহমান, প্রান্তিক চাষা )
"পৃথিবীর পিঠের ওপর গরু চরাতে গিয়ে এ জন্ম
বুঝে যায় বাঁশিটির ভেতরে কী ভাবে বিরহ কেঁপে ওঠে।"
(গরু চরাতে গিয়ে, প্রান্তিক চাষা )
সারল্যের চর্চা এবং সাবলীল ভাবে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা আপাত দৃষ্টিতে যতটা সহজ অন্তরে ততটাই কঠিন। কবিতার কাছে কবি সৎ না থাকলে, এরকম লেখা যায় না। অথচ এক প্রান্তিক চাষার ছেলে হিসেবে কবি কী অসামান্য দক্ষতায়, এবং একপ্রকার শিশুসুলভ সারল্যে বলতে পেরেছেন -
"চাষ করি খেটে খাই। এ বছর শ্রাবণ বিমুখ
তাই দারিদ্র রেখার উপর দিয়ে হেঁটে যাই
শহরে জন খাটি, এ জনমে নিজ কর্ম করি।
#
গত বছর ধান বিক্রি করে শহর থেকে
বাবার ধুতি মায়ের কাপড়
কিনে এনেছিলাম
#
এ বছর স্বপ্নে বহ্নি, তবু বেঁচে থাকি!! স্বপ্নে সপনে "
(প্রান্তিক চাষার ছেলে, প্রান্তিক চাষা )
রুদ্র পতির কবিতা লেখার শুরু যদি আশির দশকের একদম শেষ থেকে ধরা হয় তাহলে নব্বইয়ের গোড়ার কবি রুদ্র পতি। কবির প্রথম দুটি বই এবং ৯৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ে কবি প্রায় তিন হাজার কবিতা লিখেছেন এবং তারপর পরবর্তী বছরগুলিতে ২০০৮ পর্যন্ত কবির দাবি অনুযায়ী আরও তিন হাজার কবিতা লিখেছেন। যদি এই সময়টিকে তাঁর মূল রচনার সময় ধরা হয় তাহলে এই সময়ের রচনা প্রায় ছয় হাজার কবিতা। এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে, যদিও তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ততটা বেশি নয়। প্রথম দিকে দুটি বইয়ের অনেকদিন পর ২০০৪ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে আরো তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। "বেকারের কবিতা"( ওয়াবী প্রকাশনী,২০০৪), "এ বছর শ্রাবণ ভালো"(কবিতা পাক্ষিক ২০০৪), এবং "গুচ্ছমূল"(লোকসখা প্রকাশনা,২০০৫)।এই তিনটি বইয়ের মধ্যে "বেকারের কবিতা" বইটির কবিতাগুলি অনেক আগে রচিত। নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে কবি বেশ কয়েক বছর বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কবিতাগুলিতে এই বেকার জীবনের প্রতিচ্ছবি, কষ্ট, যন্ত্রণা, এবং সরকার বা ব্যবস্থার প্রতি একটি দ্রোহাত্মক মনভাবে ফুটে উঠেছে। কবি নিজের কথায় অনড় থেকেছেন। কবিতার ভাষা জোরালো হয়েছে, প্রয়োজনে কখনো প্রতিবাদে শব্দের কোমলতা হারিয়েছে।
"আজ সারারাত শুধু প্রতিবাদ
মদ খাবো?
ব্যবহৃত যোনিতে শুক্র কণাদের
ব্যাকরণ ভেঙে আজ সারারাত বিরুদ্ধ কিছু করে যাবো
#
আজ সারারাত শুধু প্রতিবাদ
আবেশের ব্যাকরণ ভেঙে, মদ নয়
কন্ঠে ঢেলে নেবো গাঢ় অ্যাসিড"
(আজ সারারাত, বেকারের কবিতা)
কবি সাবজেক্টিভ, স্পষ্ট ভাবেই একজন সাবজেক্টিভ কবি, যিনি নিজের যাপনের প্রতিটি স্তরকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজেকে তুলে ধরতে কোনরকম কুন্ঠাবোধ করেননি। নিজের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-
" চাকরি নেই কবিতার বই নেই...
কাঁথের ওপরেই রোগগ্রস্থ মা, জন্মান্ধ পিসি
....
সংসার জুড়ে হাড়ির ওপরে বেহায়া আগুন"
(ভূমিকা, বেকারের কবিতা)
এই ক্রোধ ঠিক কার প্রতি তা স্পষ্ট নয়। সিস্টেমের বিরুদ্ধে হতে পারে, হতে পারে অসহায়তার জন্য, হতে পারে কিছু করতে না পারার জন্য। আবার হতে পারে নিজের অজ্ঞ দেশবাসীর জন্য, দারিদ্রতার জন্য। এই আগুন খানিকটা অ্যাংরি ইয়াং ম্যানদের ইম্পোটেন্ট এঙ্গারের মতো। যার বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের ভাষা হয়, কিন্তু কিছু সংগঠিত রূপ দিতে পারে না। শেষে এক শূন্য হতাশা রচনা করে।
"আদিবাসী মহিলাটি পা ফাঁক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসি করে
তার ব্যাকরণ, বিচ্ছিন্নতার দিকগুলি অজানা থেকে যায়
শোষণ বুঝলো না সে.…"
(রৌরবে, বেকারের কবিতা)
অথবা কবি লিখেছেন -
" আমার বুকের রক্ত কাঁপে ঘৃণায়, অভিমানে"
(ভারতবর্ষ, বেকারের কবিতা)
কবির দ্বিতীয় পর্বে লেখা বইগুলির মধ্যে 'এ বছর শ্রাবণ ভালো" খুব গুরুত্বপূর্ণ। কবি 'প্রান্তিক চাষা' বইয়ে যে যাত্রাপথ শুরু করেছিলেন তার পূর্ণতা এই বইয়ের মধ্যে দেখতে পাই। একজন প্রান্তিক জনের অন্তরের কথা প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে এই বইয়ের কবিতাগুলিতে। আগের বইগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় এই বইয়ের কবিতাগুলিতে এক অজানা রোমান্সের সন্ধান পাই। বইয়ের শিরোনামে যে বৃষ্টির সন্ধান তা শুধু ফসল ফলানোয় সীমাবদ্ধ না থেকে এক গ্রাম্য মানুষের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া, এবং সর্বপরি এক অজানা ভালোবাসার সন্ধান হয়ে উঠেছে। রয়েছে একটা দুখঃচারণ, যা কখনোই লোক দেখানো প্রকট হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ তা হয়েছে প্রকৃত কবিতা -
" হাসি ও কান্নার মধ্যে তুমি দেখে নিও
একটি মাদলের ভালোবাসা, আমার গ্রামীণতা "
(সংসার, এ বছর শ্রাবণ ভালো)
"দুঃখদশা থেকে উঠে আসে তুমুল
জেল ভাঙা শরৎ এর মোহময় গান "
(শরৎ, এবছর শ্রাবণ ভালো )
"আলতি পাতায় মায়ের চোখের জল;
আজ রুক্ষদিন, তবু দুঃখ করব না।"
(আলতি পাতায়, এ বছর শ্রাবণ ভালো)
অথবা কখনো চাষের আনন্দে প্ৰিয় মুখ হয়েছে সোনালী ধানের ক্ষেত, অথবা জমকালো ভরাট মেঘ -
"তোমার মুখের ওপর সম্ভাবনার আলো
তোমার চোখের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি আনুক্রমিক-
হারিত, গাঢ় হারিত, সোনালী
ধানের বেড়ে ওঠা!"
(বর্ষমঙ্গল, এ বছর শ্রাবণ ভালো )
ফসলসম্ভবা ক্ষেত প্ৰিয়জনের সাথে জড়িয়ে গেছে প্রাণের গভীরে। এ লাইনগুলিকে রোমান্টিকতা বলবো না তো আর কোন লাইনকে বলবো -
" বউয়ের দুটি চোখে তখন জ্যোৎস্নারাত
বউয়ের দুটি চোখে তখন উদ্দীপ্তনার আভা "
(ধানফুল, এ বছর শ্রাবণ ভালো )
"আজ সারারাত চাঁদ তোমার শস্য পাহারায় "
( বন্যাপরবর্তী, এ বছর শ্রাবণ ভালো )
পুরো কাব্যগ্রন্থটি জুড়ে শুধু প্রান্ত ভূমে ফসল ফলানোর আনন্দ না, সাথে ঘিরে রয়েছে অন্য আরেক মাদকতা, তা হতে পারে, প্রেম, পরিণয়, দুঃখ, গ্রাম্যজীবনের সারল্য, এবং সর্বপরি এক অজানার সন্ধান, এক না পাওয়াকে পাবার আকুল স্মৃতিচারণ -
"করজোড়ে বর্ষণের আকুলতা প্রতিটি রেখায় যেন নদী পাই
প্রতিটি বিন্দুতে জলাশয় ; বহুদিন নৌকা বাইনি, বহুদিন
ঘাটে লাগেনি তরী। "
(এ বছর শ্রাবণ ভালো, এ বছর শ্রাবণ ভালো )
দ্বিতীয় পর্বে লেখা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল "গুচ্ছমূল"। নামকরণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কবি এই বইয়ের মধ্যেও কবি সেই শিকড়ের সন্ধান করেছেন, যা তাঁর নিজের। ধানের গাছির নীচে যে গুচ্ছমূল থাকে তাই কবিকে প্রেরণা দেয় সৃষ্টির, সৃজনের - যা ফসল ভর্তি ক্ষেতের মতো কবিকে গর্ভবতী করে। এক সন্তানের জন্ম দেওয়া মায়ের মতোই 'অপান্ডিত্যের' সারল্য নিয়ে কবি রচনা করে যান। আসলে অন্তরের এই অকপট শুদ্ধাচারণ, এইটা নিজেকে পাঠকের কাছে শিশুর মতো মেলে ধরায় যে আনন্দ বর্ষণ হয়, তাই হয়তো শ্রাবণের ধারা, তাই হয়তো ফসলের সুখ, তাই হয়তো প্রান্তিক চোখে 'এপিফ্যানিক' আলোকচ্ছটা - এই আলোর কাছে তথাকথিত সাফল্যের পরিসংখ্যান বড় বেমানান। কবি সেই আবহমানকে বরণ করেছেন, নিজেকে তরলতম করে-
"লিখি ধামা ভরা চাল, বাটা ভরা পান
লিখি মাঠ ভরা ধান আর গাছ ভরা আম
... .... .... .... ....
বেঁচে উঠুক লোকগান আবহমান বাংলা কবিতার ধারা "
( আনন্দ, গুচ্ছমূল)
গ্রাম্যজীবনের প্রতিচ্ছবি কবির কবিতায় যেভাবে ফুটে উঠেছে তা এককথায় অসামান্য। এই কবিতা পাঠের পর অন্য এক জগতে নিয়ে যায় -
" ঝিঙে ফুল ফুটে ওঠে ভাদ্র শেষের গোধূলি আভায়
সন্ধ্যা হলো মাগো
তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানোর সময় হলো
শাঁখে ফুঁ রাত্রের সমস্ত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে "
(নিরীক্ষণ করে দেখি, গুচ্ছমূল )
বিজ্ঞানের শব্দের ব্যবহার, একদম গ্রাম্য শব্দের পাশাপাশি এক অদ্ভূত বৈপরিত্য সূচিত করেছে, যেমন ফসলের সাথে মিশে গেছে প্রিয়তমা শরীরে, এ যেন যাপিত-জীবন কবিতা-জীবনর সাথে বিশুদ্ধ সঙ্গমে লীন -
"দশমিক ডান পাশে দিয়ে তোমার মান বাড়িয়ে দিই
যখন ধানফুল হাওয়ায় এবং জলে ভেসে যায়
এবং ধানের থোড় তার সম্পূর্ণতা প্রকাশ করেছে দেখলাম
সফল এ জন্মে তাই জ্যোৎস্না প্রভাবিত
ধানফুল তোমার উঠোনে তোমার বিছনায় এসে পড়ে
ধীরে ধীরে তোমার নিপিলের চারপাশ কালো হয়
ভেলা পড়ে
শরীরে শরীর জাগে "
(দশমিক বিন্দুর ব্যবহার, গুচ্ছমূল )
চাষার জীবনে শুধু আনন্দ না, অভাবের আঁধার, ভাদরের কষ্টের দিন বড় সত্যি। এই সত্যকে কবি উপেক্ষা করে যান নি। বড় স্পষ্ট করে লিখে গেছেন। তিনটে কবিতার কিছু পঙক্তি তুললাম এখানে -
"টানের সংসার।গোরু দুটি বিক্রি করা ছাড়া আর উপায় রইল না।
খড় নেই, মাটিও পুড়ে লাল..."
( অভিমান, গুচ্ছমূল )
"পাগল করা খিদে এলো। ভাদ্র মাস হাহাকার তোলে;
দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দোকানি চলেছে দূরে
খরিদ্দারেরা আগেই চলে গিয়েছে পুব দিকে, শহরে...."
(শরৎ, গুচ্ছমূল )
"বাড়িতে চাল নেই ভাদ্রমাস কৃষকের গ্রাম
গ্রামে বসত করে চাল ফুরিয়েছে বলতে নেই
তাই মা বলে - চাল বেড়েছে
এতে নাকি মা লক্ষ্মী খুশি হন..."
(ভয়, গুচ্ছমূল )
প্রান্তিক কবি রুদ্র পতি আত্মজৈবনিক, সাবজেক্টিভ, এবং অবশ্যই রোমান্টিক। তিনি নিজের জীবনকেই তুলে ধরেছেন, ধার ধরেন নি স্মার্ট কবিতার, বা চটকদারি লাইন বা শব্দের ব্যবহারে। এখানেই কবিতার জয়, এখানেই সার্থকতা। কবির এই কবিতার অংশ পড়ে থেমে যেতে হবে যে কোনো নিবিড় পাঠককে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত -
"আলো এসে ফিরে গেল আমরা দুজনাই
ধরতে পারলাম না, তাই অন্ধকারে ডুবে যায় বসত
আমার জন্মান্ধ জ্যাঠা ও পিসির চোখে আলো নেই
শুধু অনুমানে পথ চলে যেমন উইপোকা অথবা কেঁচো "
(ক্ষত, গুচ্ছমূল )
"গুচ্ছমূল" কাব্যগ্রন্থের পর কবির আর কোনো কবিতার বই প্রকাশ পায় নি। তিনি লিখে গেছেন কিন্তু প্রকাশের গতি মন্থর হয়েছে। কবির তরুণ বয়সে প্রকাশের আনন্দ শিথিল হয়েছে। মাঝে বেশ কয়েক বছর কবি একটা স্বেচ্ছা নির্বাসনও নিয়েছেন ।এক অদ্ভুত উদাসীনতা লক্ষ করা গেছে কবির মধ্যে। ২০১৬-১৭ সালের পর থেকে কবিকে আরও নতুন ভাবে দেখা যায়। প্রশ্ন একটাই, সেই পুরনো কবিকে আমরা কী পাবো আবার নতুন ভাবে, নতুন রূপে? এখন শুধু এটুকু বলার কবি মুছে যায় না, তাঁর কবিতাগুলিও ফিনিক্স পাখির মতো প্রতি শ্রাবণে আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সে অমরত্ব, এই সে আবহমান!
সূত্র :
১.প্রান্তিক চাষা, সিন্ধুসারস প্রকাশনী, হাওড়া, ১৯৯৩
২.লেদ অথবা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, খনন প্রকাশন, নাগপুর, মহারাষ্ট্র, ১৯৯৩
৩.বেকারের কবিতা, ওয়াবী প্রকাশনী, আসনবনী, বাঁকুড়া ২০০৪
৪.এ বছর শ্রাবণ ভালো, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা, ২০০৪
৫.গুচ্ছমূল, লোকসখা প্রকাশনা, কলকাতা, ২০০৫
৬.রুদ্র পতি : সাক্ষাৎকার, রাহুল গাঙ্গুলী, তরঙ্গ পরিবার https://tarangahouse.blogspot.com/2017/11/blog-post_96.html?m=1
৭. মেঠো কবিতা, নিশীথ রায় চৌধুরী, প্রান্তিক ৬৭-৬৮, ২০০৬
৮. হোয়াটস অ্যাপ কথাপোকথন, রুদ্র পতি- সুপ্রিয় দেওঘরিয়া,২০২৪





.jpeg)